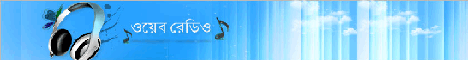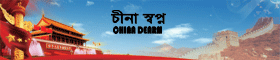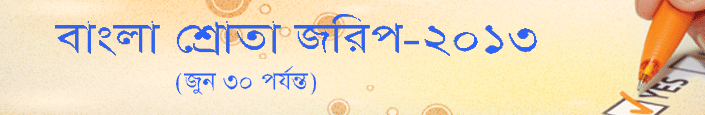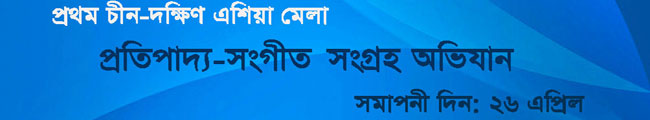এ পরিকল্পনায় পোশাক কারখানার পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি কারখানার পরিবেশ ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং প্রশিক্ষণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে যেসব কারখানা শ্রম পরিবেশ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বা ভবন নিরাপত্তার বিষয়গুলো লঙ্ঘন করবে তাদের রফতানি সনদ বাতিলের কথাও বলা হয়েছে এই 'কর্মপরিকল্পনায়'।
গত ২৮ জুন বাংলাদেশের জিএসপি 'স্থগিতের' ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।
সব পোশাক কারখানার শ্রমিক, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং পরিদর্শকের প্রতিবেদনসহ একটি উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডার তৈরির আহ্বানও রয়েছে এ 'কর্মপরিকল্পনায়'। এ বিষয়গুলো লঙ্ঘনকারী কারখানার নাম, ওই কারখানাগুলোর ওপর আরোপিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থার পর কারখানার সংশোধনের তথ্যও এই তথ্যভাণ্ডারে রাখার কথা বলা হয়েছে।
যে কারখানা পরিদর্শকের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হবে তার নামও এতে রাখতে হবে। 'কর্মপরিকল্পনায়' প্রতিটি শিল্পকারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে ওবামা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।
গত ২৪ এপ্র্রিল রানা প্লাজা ভবন ধসে ১,১২৯ শ্রমিকের মৃত্যু ও নভেম্বরে তাজরিন ফ্যাক্টরিতে আগুনে ১১২ জন নিহত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বাংলাদেশের বাণিজ্য সুবিধা স্থগিত করে। পোশাক কারখানার প্রসঙ্গে ওবামা প্রশাসন থেকে বলা হয়, বাংলাদেশের উচিত পোশাক কারখানার শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে ইউনিয়ন গঠনে মনোযোগী হওয়া।
জিএসপির আওতায় বাংলাদেশ প্রায় পাঁচ হাজার পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধায় যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করত। তবে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় পাঁচশ কোটি ডলারের যে পণ্য রফতানি করে থাকে তার মাত্র এক শতাংশ জিএসপির আওতায় পড়ে। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিপণ্য তৈরিপোশাক যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধার আওতায় পড়ে না।
এদিকে জিএসপি বাতিলের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই একটি নতুন শ্রম আইন করেছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী দ্য নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা এটাকে হাফ-হার্টেড বা আধা-আন্তরিক বলে আখ্যায়িত করেছে। পত্রিকাটির মতে, নতুন আইনটি বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে কর্মরত ৪০ লাখ শ্রমিককে বিপজ্জনক কর্মপরিবেশ থেকে খুব কমই সুরক্ষা দেবে। সে জন্য ইউরোপ-আমেরিকাকে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর চাপ আরও বাড়াতে হবে।
বুধবার প্রকাশিত পত্রিকারটির এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে বিরাজমান সমস্যাবলির সমাধানে শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে। শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন সহজ করার লক্ষ্যে শ্রম আইন পরিবর্তন করা হলেও তাতেও এখনও অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে। পত্রিকারটির মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভবনধস, অগ্নিকাণ্ডসহ অন্যান্য কারণে শত শত মানুষের দুঃখজনক মৃত্যুর যেসব ঘটনা ঘটেছে, সে ধরনের পরিস্থিতি রোধে যতটা পদক্ষেপ থাকা প্রয়োজন ছিল, তা নেই আইনটিতে।
নিউইয়র্ক টাইমস মনে করছে, নতুন আইনে ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা পোশাকশিল্পের মালিকদের রাখা হয়নি, যেটি আইনটির একটা ভালো দিক। কিন্তু এতে আবার শ্রমিককের ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রেও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, কারখানার নিজস্ব শ্রমিকদের মধ্য থেকেই ইউনিয়নের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে, বাইরের শ্রমিকেরা এতে জড়িত থাকতে পারবেন না। এর ফলে মালিকপক্ষ যাঁদের পছন্দ করবে না, তাঁদের নিছক চাকরি থেকে বাদ দিয়ে শ্রমসংঘ করার প্রক্রিয়া দুর্বল করে দিতে পারবে।
নিউইয়র্ক টাইমস অবশ্য স্বীকৃতি দিয়েছে যে, গত এপ্রিল মাসে একটি কারখানা ভবস ধসে এক হাজার এক শরও বেশি শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পোশাকশিল্পে নিরাপত্তার যে ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণের চেষ্টা করে আসছে। আর বাংলাদেশ হচ্ছে ওয়াল-মার্ট, গ্যাপ ও এইচঅ্যান্ডএমের মতো পশ্চিমা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পোশাকপণ্যের বড় সরবরাহকারী।
আইনটিতে বলা হয়েছে, কেউ কারখানার মোট শ্রমিকের ন্যূনতম ৩০ শতাংশের ভোট না পেলে সরকার ওই প্রতিষ্ঠানে শ্রমসংঘ অনুমোদন করবে না। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো কোম্পানির এক কারখানা আরেকটি থেকে অনেক দূরে হলে ভোট চাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।
পত্রিকাটির মতে, বাংলাদেশের সংশোধিত শ্রম আইনটি আসলেই রক্ষণশীল। কারণ এতে বিশেষ রপ্তানি অঞ্চলগুলোয় অবস্থিত কারখানাগুলোয় শ্রমসংঘ করার অনুমতি দেওয়ার বিধান রাখা হয়নি। এ ছাড়া কোনো কারখানায় ধর্মঘট ডাকতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিকের সমর্থন থাকতে হবে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের উদ্ধৃতি দিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, এ আইন অনুযায়ী সরকার যদি শ্রমিক ধর্মঘটকে জনজীবনের জন্য কষ্টকর ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে, তাহলে তা বন্ধ করে দিতে পারবে।
তবে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা আশা করছেন, নতুন আইনটি ওবামা প্রশাসন ছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যিক সুবিধা বাতিল করার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখবে। তাঁরা মনে করছেন, বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সামনে সম্ভাবনা বিপুল।
বিশ্লেষকদের মতে, ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি অন্তত ৩৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে। কারণ বিশ্বের বর্তমান মোট ৪১২ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাকের বাজারের মধ্যে বাংলাদেশের দখলে মাত্র ৪.৮ শতাংশ। বাংলাদেশের বৃহত্তম দুই রফতানি বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ খাতের মোট রফতানির ৮৬ শতাংশ যায়, যা তাদের মোট চাহিদার মাত্র ৬ শতাংশ। বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান সংকট কাটাতে এবং সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকার, সরবরাহকারী, ক্রেতা এবং শ্রমিকদের একসঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়নযোগ্য কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। (এসআর)
| ||||